বিংশ শতাব্দীততে যে কয়েকজন কথা সাহিত্যিক বিশ্বকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিলো, ফরাসি দার্শনিক ও সাহিত্যিক আলবেয়ার কাম্যু (১৯১৩-১৯৬০) সেই বিরলপ্রজাদের একজন। তার লেখা “দ্যা আউটসাইডার” উপন্যাসটি তার অন্য সব উপন্যাস গুলোর থেকে একটু বেশি আলাদা এবং বেশ জনপ্রিয়। ফরাসি ভাষায় উপন্যাসটির আসল নাম হলো “লেত্রঁজে”। মুলতো অস্তিত্ববাদের উপর ভিত্তি করে উপন্যাটি রচিত হয়েছে। অবশ্য ক্যামুর বেশি ভাগ লেখায় অস্তিত্ববাদ ও ব্যাক্তিস্বাধীনতার উপস্থিতি পাওয়া বেশি লক্ষ করা যায়। এই উপন্যাসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। উপন্যাসের মুল গল্পটি মঁসিয়ে ম্যুরসল্ট নামের এক সাধারন ফরাসি চাকরিজীবী যুবকে ঘিরে গড়ে তুলা হয়েছে এবং লেখক নিজেই সেই ম্যুরসল্ট এর ভুমিকা পালন করেছে। মানে ফার্স্টপার্স ন্যারেটিভ পদ্ধতি রিতিতে পুরো গল্পটি বলা হয়েছে।
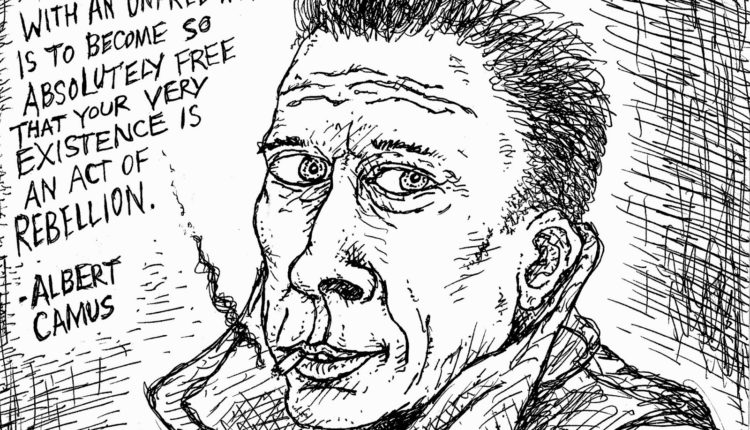
এই উপন্যাসটি বেশিকিছু লাইন এখন বিশ্বজোড়া বিখ্যাত, যেমন উপন্যাসের শুরুতে লেখা আছে “মা মারা গেছেন আজ অথবা গতকাল, ঠিক ধরতে পারছি না”, ফলে পাঠকের কাছে প্রথম থেকে গল্পের প্রধান চরিত্র ম্যুরসল্টকে একটু অদ্ভুত লাগবে। উপন্যাসটির আর একটু ভেতরে গেলে তাকে আরো বেশি অদ্ভুত মনে হবে। কারণ মায়ের মৃত্যুতে ও ম্যুরসল্টের আচরনে কোন শোকেরর ছায়া পাওয়া যায় না। সে দিব্যি তার মায়ের লাশের সামনে বসে ধূমপান করে। দাফনকাজ শেষ করেই আবার সে গ্রাম থেকে শহরে ফিরে আসে, মায়ের কবরের পাশে বসে শোকার্ত না হয়ে বরং আগামীকাল সকাল বারোটা প্রর্যন্ত সে ঘুমাতে পারবে ফিরতি পথে এ কথা ভেবে সে মনে মনে খুশি হয়। সেজন্য বোধ হয় অনেক পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টিতে ম্যুরসল্ট পৃথিবীর সব আলোচিত উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র থেকে একটু বেশি আলাদা এবং জটিল ও অদ্ভুত চরিত্র। যাকে বিশ্লেষণ করা খুব কঠিন। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়েছে যেসব পাঠক ও সমালোচক অস্তিত্ববাদ এ বিশ্বাসী তাদের কাছে ম্যুরসল্ট একটি সহজ ও সাধারন চরিত্র মনে হবে। কারণ অস্তিত্ববাদ মনে করে সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্য মানুষের সত্ত্বা বা অধিবিদ্যা ধারনার কোন প্রয়োজন নেই। এছাড়া তা মানুষের জীবনের সুখ পরিপূর্ণ ভাবে প্রদান করে না। মানুষের জন্য দরকার নিজের অস্তিত্বকে স্বীকার করা।
শুধুমাত্র অস্তিত্ব স্বীকার হলেই মানুষের জীবনের সত্য অর্জিত হয়, কারণ মানুষ সবসময় মুলত স্বাধীন এবং একা। তাই স্বাধীনতা মানুষকে সবকিছু চিনতে, ভাবতে ও অর্জন করতে শেখায়। ম্যুরসল্ট ঠিক তেমনি একজন স্বাধীনচেতা যুবক। সম্পূর্ণ উপন্যাসে মুলত এটা বোঝানো হয়েছে যে সামাজের অধিকাংশ মানুষ যেটা সত্যি মনে করে সেটা আসলে সত্যি না, আবার মিথ্যাও না। কিন্তু সামাজিক বিশ্বাসের বাইরে গেলেই যে সে অদ্ভুত এমন দাবি মোটেই যুক্তিযুক্ত না। কারণ মায়ের মৃত্যুতে না কাঁদতে জানা মানুষ আবেগহীন এটা যেমন সত্য পাশাপাশি সে অস্তিত্ববাদে বিশ্বাসী একজন সুখি ও সুন্দর চিন্তার মানুষ সেটাও তেমন সত্য। কারণ অন্য মানুষের ভেতর আবেগের চেয়ে ভান করার প্রবনতা বেশি থাকে, কিন্ত ম্যুরসল্ট এমন একজন মানুষ যার ভেতর আবেগ আছে অথচ ভান করা তার অভ্যাসে নেই। ফলে মায়ের মত্যুর পর সে খুব সহজে শহরে ফিরে আসে এবং পূর্বের মতো স্বাভাবিক জীবন শুরু করে। এরপর দেখা যায় উপন্যাসের মাঝামাঝিতে একজন আরবীকে খুন করে সে। অবশ্য নিজেকে বাঁচানোর জন্য এছাড়া তার কাছে অন্যকোন উপায় ছিলো আবার ছিলো না কিন্তু তখন সেটা ভাবার মতো পরিবেশও সেখানে ছিলো না।
পরিতাপের বিষয় এই যে, আদলতে দাঁড়িয়ে ম্যুরসল্টকে যেসব প্রশ্নের মুখামুখি হতে হয় তার সাথে এই খুনের ঘটনার সম্পর্ক কি সেটা বুঝতে উঠতে ম্যুরসল্টের কষ্ট হলো। কেন সে মায়ের মৃত মুখটা শেষবারের জন্য দেখতে চেয়েছিলো না? কেন সে গির্জায় মায়ের লাশের সামনে বসে ধূমপান করেছিলো? কেনো শবযাত্রায় কেউ তাকে মায়ের লাশে পাশে বসে কাঁদতে দেখেছিলো না? এগুলো ছিলো সেখানে প্রধান প্রশ্ন! যদিও বাস্তবি ভাবে এসব প্রশ্নমালা এই খুনের ঘটনা বিচারের জন্য অপ্রাসঙ্গিক। তবুও আদলতে ফরাসি উকিল অবশেষে বিচারকর্তার উদেশ্য বলেছিলে “যে ব্যক্তি মায়ের শবযাত্রায় কাঁদে না, আমাদের সমাজ মনে করে তাকে মৃত্যদন্ড দেয়া উচিত’। এই বিচারকাজটা অন্য পাঠকের কাছে কেমন মনে হবে তা আমি জানি না তবে আমার কাছে মনে হয়েছে খামখেয়ালিপূর্ন ।

তবে আমি শুধু এটুকুই বোঝাতে চেয়েছি যে, উপন্যাসটির নায়ককে অভিযুক্ত করার কারণ ছিলো সে আর সবার মতো সমাজের গড্ডালিকা-প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয় না। এই অর্থে সে সমাজের কাছে একজন বাইরের লোক, একজন আগন্তুক।এছাড়া সে যেন জীবনের পাড় ঘেষে হাঁটছে, শহরের নয় বরং শহরতলীতেই তার উপস্থিতি, একাকী এবং অনুভূতিপ্রবণ। একারণেই হয়তো কোন কোন পাঠক তাকে পতিত বলেও মনে করে থাকেন। কিন্তু এই চরিত্রকে আরো ভালো করে বুঝতে হলে, অন্তত লেখকের মনে যে ছবিটি ছিল তা আরেকটু স্পষ্ট করে জানতে হবে এবং নায়ক মরসোঁ ঠিক কোন পন্থায় সমাজের সবাই যা করে চলেছে তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তা বুঝতে হবে। শুধুমাত্র যা সত্য নয় সেটা বলাই মিথ্যা নয়, সত্যকে বাড়িয়ে বলাটাও একপ্রকার মিথ্যা। মাঝে মাঝে এমনও হয়ে থাকে যে একজন মানুষ তার হৃদয়ে যেটুকু অনুভব করছে তারচেয়ে বেশী প্রকাশ করছে ফলে সেটা আরেক ধরনের মিথ্যা বলা। সুতারাং জীবনকে সরলতর করতে আমরা সবাই প্রতিটি দিনই নিজের অজান্তে এমন কাজ করে থাকি। কিন্তু মরসোঁ জীবনকে সরলতর করতে চায়নি। সে নিজে যা, শুধু সেটাই সে আদলতে বলেছে। উকিলের পরামর্শ উপেক্ষা করে নিজের অনুভূতিকে আড়াল করতে সে অস্বীকৃতি করেছিলো। আর এর ফলে করে সমাজ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং আদলত তাকে সময়োচিত রীতি মেনে কৃত অপকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে বলেছিলো, কিন্তু সে উত্তরে বলেছিলো,” এ ধরনের কাজে সে অকৃত্রিম অনুশোচনার জায়গায় সে বিরক্তি বোধ করে”। আর তার এই ন্যুয়াঁস-ই তাকে সমাজের চোখে নিন্দিত করে তুলেছিলো । তাই, ম্যুরসল্টকে পতিত, জটিল,না বলে বরং একজন দুঃখী এবং অনাবৃত মানুষ বলাটাই যুক্তিযুক্ত হবে বলে মনে হয়। কারণ ম্যুরসল্ট এমন এক সূর্যকে ভালোবাসে যার আলো দূর করে দেয় সব ছায়া এবং তাকে একজন আবেগ বিবর্জিত মানুষ মনে করাটাও ঠিক হবে না। সুতারাং সে এক অবিচল ও নিগূঢ় ভালোবাসা দ্বারা তাড়িত যার ভালোবাস পরমসত্যের প্রতি জীবন ও অনুভূতিজাত যে সত্য আজোও সমাজের চোখে ক্ষতিকর মনে হলেও, সেটাকে বাদ দিয়ে আত্মজয় কিংবা বিশ্বজয় কখনোই সম্ভব হবে না।
তথ্যসূত্র : দি আউটসাইডার (অনুবাদ“মুহম্মদ আবু তাহের) উকিপিডিয়া“লেত্রঁজে ” মাসিক উত্তরাধিকার


para que sirve el medicamento zofran
patients who are prescribed olanzapine (zyprexa) should be monitored for
generic terbinafine 250mg – buy diflucan without prescription buy cheap griseofulvin
ezetimibe zetia